ফেসবুক এখন শুধু যোগাযোগের মাধ্যম নয়; এটি আমাদের দৈনন্দিন জীবনের গুরুত্বপূর্ণ তথ্যভান্ডারও। রাজনীতি, স্বাস্থ্য, প্রযুক্তি কিংবা বিনোদন—সব ধরনের খবর মুহূর্তেই ভাইরাল হয়ে যায় এই মাধ্যমে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, প্রতিদিন আমরা যে তথ্যগুলো দেখি, সেগুলো কি সব সত্য? ফেসবুকে ভুয়া তথ্য বা গুজব ছড়িয়ে পড়ার ঘটনা নতুন কিছু নয়। তাই যে কোনো তথ্য বিশ্বাস করার আগে সেটি যাচাই করা অত্যন্ত জরুরি। কিন্তু কীভাবে করবেন এই তথ্য যাচাই? আসুন, জেনে নেওয়া যাক ফেসবুকে তথ্য যাচাইয়ের কার্যকর কিছু উপায়।
উৎস যাচাই: কে শেয়ার করেছে?
তথ্য যাচাইয়ের প্রথম ধাপ হলো উৎস যাচাই করা। ফেসবুকে অনেক সময় ব্যক্তিগত অ্যাকাউন্ট থেকে বিভিন্ন খবর শেয়ার করা হয়, যা নির্ভরযোগ্য নাও হতে পারে। যদি কোনো তথ্য সত্যি হয়, তাহলে সেটি সাধারণত সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত হয়। তাই প্রথমে দেখুন, খবরটি কোনো বিশ্বাসযোগ্য গণমাধ্যম প্রকাশ করেছে কিনা। যদি তথ্যটি শুধু অচেনা পেজ বা অ্যাকাউন্ট থেকে আসে, তবে সেটি গুজব হওয়ার সম্ভাবনা বেশি।
যে তথ্যটি পেলেন, সেটি কার কাছ থেকে এসেছে? বিখ্যাত সংবাদমাধ্যম (যেমন BBC, প্রথম আলো, বিবিসি বাংলা) বা সরকারি প্রতিষ্ঠান নিশ্চিত করেছে কি না, তা দেখুন। যদি পোস্টদাতা কোনো নামহীন আইডি বা সন্দেহজনক পেজ হয়, তাহলে সেটি এড়িয়ে চলুন।
২০২০ সালে ফেসবুকে একটি পোস্ট ভাইরাল হয়েছিল—”লবঙ্গ দিয়ে করোনা সম্পূর্ণ নির্মূল সম্ভব!” অনেকেই বিশ্বাস করে এই তথ্য শেয়ার করেন। পরে জানা যায়, এটি একটি নামহীন ফেসবুক পেজের বানানো গুজব, যার পেছনে কোনো বিজ্ঞানসম্মত ভিত্তি ছিল না।
চটকদার শিরোনাম দেখলেই শেয়ার নয়!
অনেক সময় ক্লিকবেইট (Clickbait) বা আকর্ষণীয় শিরোনাম দিয়ে মানুষকে ভুল তথ্যের দিকে আকৃষ্ট করা হয়। “অবিশ্বাস্য ঘটনা! আপনি জানলে চমকে যাবেন”—এ ধরনের শিরোনাম দেখে সন্দেহজনক মনে হলে বিস্তারিত পড়ার আগে উৎস যাচাই করুন। প্রয়োজনে অন্য বিশ্বস্ত সূত্রে যাচাই করুন।
২০২৩ সালে এক পোস্টে লেখা ছিল—”ভয়ংকর! আগামীকাল থেকে মোবাইল ইন্টারনেট বন্ধ!” অনেকেই এটি না পড়েই শেয়ার করেছিলেন। কিন্তু পরে জানা যায়, এটি ছিল ক্লিকবেইট শিরোনাম, যার উদ্দেশ্য ছিল শুধু ভিউ বাড়ানো।
ছবি বা ভিডিও আসল নাকি পুরোনো?
ফেসবুকে অনেক সময় পুরোনো ছবি বা ভিডিও নতুন ঘটনার সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়, যা বিভ্রান্তিকর হতে পারে। আপনি ছবি বা ভিডিও যাচাই করতে গুগল রিভার্স ইমেজ সার্চ (Google Reverse Image Search) বা টিনআই (TinEye) ব্যবহার করতে পারেন।
২০২১ সালে বাংলাদেশের বন্যার সময় ভারতের একটি পুরোনো বন্যার ছবি ব্যবহার করে বলা হয়েছিল—”বাংলাদেশের ভয়াবহ অবস্থা!” পরে গুগল রিভার্স ইমেজ সার্চ করে দেখা যায়, ছবিটি ২০১৭ সালের আসামের বন্যার।
ক্রস-চেকিং করুন: একাধিক সূত্রে তথ্য মিলিয়ে নিন
একটি নির্দিষ্ট তথ্য যদি সত্যি হয়, তাহলে তা সাধারণত একাধিক বিশ্বস্ত সংবাদমাধ্যমে পাওয়া যাবে। আপনি যদি কোনো গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পান, তাহলে সেটি অন্য সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে কিনা, তা দেখে নিন। একটি চাঞ্চল্যকর খবর পেলে BBC, CNN, BBM-র মতো প্রতিষ্ঠিত সংবাদমাধ্যমে খুঁজে দেখুন।
২০২২ সালে ছড়ায় যে, “নির্বাচনের দিন ঢাকায় কারফিউ জারি হবে!” অনেকেই ভয়ে পোস্টটি শেয়ার করেন। পরে দেখা যায়, কোনো বিশ্বস্ত সংবাদমাধ্যম এ ধরনের তথ্য দেয়নি।
আবেগের ফাঁদে পড়বেন না!
ভুয়া খবর বা গুজব ছড়ানোর ক্ষেত্রে অনেক সময় আবেগপূর্ণ ভাষা ব্যবহার করা হয়, যেমন—“এটি শেয়ার করুন, নইলে বিপদ!”, “শিগগির জানুন, নইলে দেরি হয়ে যাবে!”—এ ধরনের ভাষার ব্যবহার সন্দেহজনক।
একটি পোস্ট ভাইরাল হয়েছিল—”এই পোস্ট শেয়ার করলে আপনার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে সুসংবাদ আসবে!” এটি একটি সাধারণ ভুয়া কৌশল।
ফ্যাক্ট-চেক ওয়েবসাইট ব্যবহার করুন
বর্তমানে অনেক ফ্যাক্ট-চেকিং ওয়েবসাইট রয়েছে, যেখানে বিভিন্ন ভাইরাল তথ্য যাচাই করা হয়। বাংলাদেশে ‘বিডি ফ্যাক্টচেক’ এবং আন্তর্জাতিকভাবে ‘স্নোপস’ (Snopes), ‘ফ্যাক্টচেক.অর্গ’ (FactCheck.org) ও ‘পলিটিফ্যাক্ট’ (PolitiFact) বেশ জনপ্রিয়।
২০২৩ সালে প্রচার হয় যে, “সরকার ১০,০০০ টাকা করে দিচ্ছে!” পরে BD FactCheck যাচাই করে জানায়, এটি প্রতারণামূলক স্ক্যাম।
বেশি শেয়ার বা লাইক মানেই সত্য নয়!
অনেক মানুষ একটি পোস্ট শেয়ার বা লাইক করলেই তা সত্যি হয়ে যায় না। গুজবও দ্রুত ছড়ায়। তাই শুধু শেয়ার সংখ্যা দেখে বিশ্বাস না করে বরং তথ্য যাচাই করে নিন।
২০২২ সালে ভাইরাল হয়েছিল—”বাংলাদেশি ছাত্র নোবেল পুরস্কার জিতেছেন!” কিন্তু পরবর্তীতে দেখা যায়, এটি একেবারেই মিথ্যা তথ্য।
সন্দেহ হলে রিপোর্ট করুন
আপনি যদি নিশ্চিত হন যে কোনো তথ্য ভুয়া, তাহলে সেটি রিপোর্ট করুন। ফেসবুকে “Report” অপশন ব্যবহার করে ভুয়া তথ্য ছড়ানো পোস্টের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া যায়।
২০২৩ সালে “বিনামূল্যে সরকারি ভাতা” নামে একটি স্ক্যাম লিংক ভাইরাল হয়। কিন্তু অনেকে ফেসবুকে রিপোর্ট করায়, ফেসবুক এটি সরিয়ে নেয়।
একটি ভুয়া পোস্টের কারণে গুজব ছড়িয়ে যেতে পারে, যার ভয়াবহ পরিণতি হতে পারে। তাই ফেসবুকে যেকোনো তথ্য যাচাই না করে শেয়ার করা থেকে বিরত থাকুন। যদি সত্য-মিথ্যা নিয়ে সন্দেহ থাকে, তাহলে উপরের কৌশলগুলো অনুসরণ করুন। আপনি সচেতন হলে অন্যরাও সুরক্ষিত থাকবে।
তাহলে এবার বলুন, আপনি আজ থেকে কীভাবে তথ্য যাচাই করবেন?


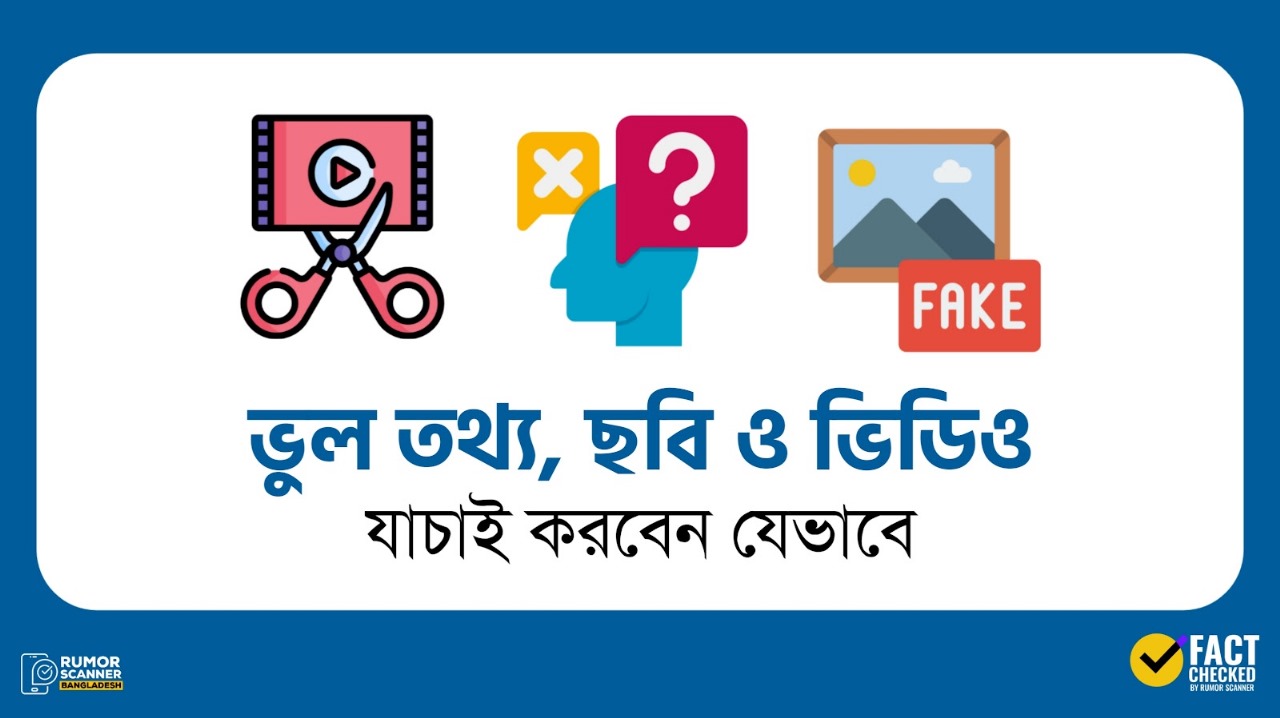



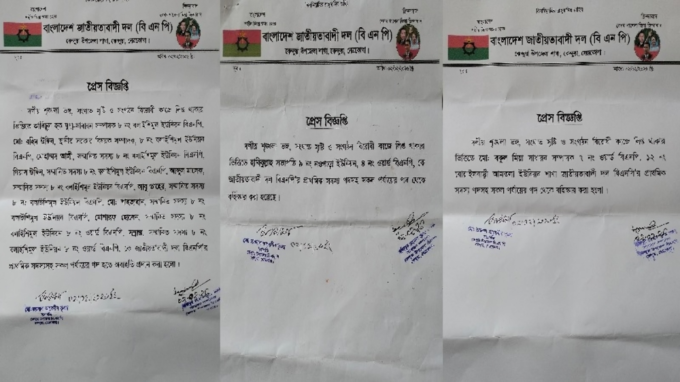




Leave a comment