
ভারতের বর্তমান পরিস্থিতি যেন এক অনিশ্চিত দ্বিধার দোলাচলে দাঁড়িয়ে। রাস্তাঘাটে, সংবাদমাধ্যমে কিংবা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে — সর্বত্র যুদ্ধের গন্ধ। অনেকে বলছেন, ‘এবার যুদ্ধ হবেই’; আবার কেউ কেউ বলছেন, ‘এখন নয়’। যুদ্ধ করা কি ভারতের পক্ষে সম্ভব ও যুক্তিযুক্ত — এই প্রশ্ন এখন তীব্র বিতর্কের কেন্দ্রে। সমরবিশেষজ্ঞ প্রবীণ সাহানির পর্যবেক্ষণ থেকে এ বিষয়ে উঠে এসেছে একাধিক সতর্কবার্তা, যা যুদ্ধকামিতার বিপরীতে এক বাস্তবসম্মত চিত্র হাজির করছে।
প্রবীণ সাহানি, যিনি ফোর্স পত্রিকার সম্পাদকও, সম্প্রতি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে স্পষ্ট ভাষায় জানান, ভারত এখন যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত নয় — অন্তত চীন ও পাকিস্তানের সম্ভাব্য যুগ্ম প্রতিক্রিয়ার মুখে। চীন বহুদিন ধরেই পাকিস্তানের সার্বভৌমত্ব রক্ষার পক্ষপাতী। ২০১৯ সালে কাশ্মীরের বিশেষ মর্যাদা বাতিলের পর থেকেই চীন এ বিষয়ে আরো সক্রিয় হয়েছে। ফলে, যদি ভারত পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধ শুরু করে, তবে চীন সীমান্তেও ‘গ্রে জোন অ্যাকটিভিটি’-র (যুদ্ধ নয়, কিন্তু যুদ্ধের মতো চাপ) মাধ্যমে জটিলতা বাড়াতে পারে। এতে ভারতের কৌশলগত প্রস্তুতি বিভ্রান্তির মুখে পড়বে—পূর্ব সীমান্ত থেকে সম্পদ সরিয়ে পশ্চিম সীমান্তে কেন্দ্রীভূত করা কঠিন হয়ে উঠবে।
এছাড়াও ভারতের আরেকটি দুর্বলতা হলো, তার উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় সীমানা। মিয়ানমার ঘেঁষা সীমান্ত, বিশেষ করে মণিপুর পরিস্থিতি, অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ব্যবস্থায় চাপ তৈরি করেছে। সেখানে আড়াই শতাধিক প্রাণহানির পরও সেনা সরানো যাচ্ছে না। ফলে পাকিস্তান সীমান্তে দ্রুত সেনা মোতায়েন কঠিন।
অর্থনৈতিক দিক থেকেও যুদ্ধ ভারতের জন্য দুঃস্বপ্ন ডেকে আনতে পারে। যুক্তরাষ্ট্রের ‘কস্ট অব ওয়ার’ রিপোর্ট অনুযায়ী, আফগানিস্তান যুদ্ধ ২০ বছরে খরচ করিয়েছে ২.৩১ ট্রিলিয়ন ডলার। রাশিয়ার ইউক্রেন যুদ্ধের দৈনিক ব্যয় প্রায় ২৮৯ মিলিয়ন ডলার। ভারত এই মুহূর্তে বিশ্বে দ্রুততম অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির দেশ—৭ শতাংশ হারে জিডিপি বাড়ছে। যুদ্ধ শুরু হলে এই প্রবৃদ্ধির ধারাবাহিকতা রক্ষা করা একপ্রকার অসম্ভব। তুলনামূলকভাবে, পাকিস্তানের অর্থনীতি এতটাই দুর্বল যে ‘ডন’ পত্রিকা বলছে, তারা এখন ‘সিঁড়ির একেবারে নিচে নেমে গেছে।’ তবে একটি বিপর্যস্ত দেশ হারানোর মতো তেমন কিছু না থাকায়, সংঘাতে প্রবেশে পিছপা না-ও হতে পারে।
ভারতের যুদ্ধ না করার নীতির উদাহরণও আছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি গত ১১ বছরে অন্তত দুইবার—পুলওয়ামা হামলা ও গালওয়ান সংঘর্ষের পর—যুদ্ধের সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও পরিপূর্ণ যুদ্ধের রাস্তায় যাননি। তবে এবার ভিন্ন পরিস্থিতি। হিন্দু জাতীয়তাবাদী মহলের প্রবল চাপ রয়েছে—‘বালাকোট বা সার্জিক্যাল স্ট্রাইক যথেষ্ট নয়’, এবার চাই কার্যকর পাল্টা আঘাত, অর্থাৎ যুদ্ধ।
এই চাপের উৎস ভারতের ভেতরের রাজনৈতিক বাস্তবতা। উগ্র জাতীয়তাবাদ এখন শুধু সংখ্যালঘু নিপীড়নে সীমাবদ্ধ নেই, বরং অন্য দেশের ওপর প্রভাব বিস্তারের চেষ্টায়ও লিপ্ত। সমাজবিজ্ঞানী ইন্দ্রনীল চক্রবর্তীর ভাষায়, এটি ‘সাংঘাতিক বিপজ্জনক’ রূপ নিচ্ছে। জাতীয়তাবাদ এখন রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ন্যায়বিচারের হাতিয়ার না হয়ে পরিণত হয়েছে পরিচয়ের রাজনীতির একটি সহিংস বাহনে।
এই রাজনৈতিক চাপের ফলে, পাকিস্তানের সঙ্গে আলোচনায় বসার সম্ভাবনাও ক্ষীণ। হিন্দু জাতীয়তাবাদী সমর্থকরা এমন আলোচনা মেনে নেবেন না, বিশেষ করে পেহেলগামের সাম্প্রতিক হামলার পরে, যার দায় একে অপরের ওপর চাপালেও কাশ্মীরের ‘স্বাভাবিকতা’ নিয়ে মোদির সরকার যে প্রচারণা চালিয়েছিল, সেটি ধাক্কা খেয়েছে।
সাবেক ‘র’ প্রধান এ এস দুলত স্পষ্ট করে বলেছেন—‘সব জায়গায় পুলিশ বসানো সম্ভব নয়’। তাহলে প্রশ্ন উঠে, এই মিথ্যাচার বা অতিরঞ্জিত শান্তিপূর্ণ চিত্র উপস্থাপনের দায় কার? পর্যবেক্ষকদের মতে, পাকিস্তানের সঙ্গে আলোচনা ব্যতীত কাশ্মীরের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা কঠিন।
কিন্তু বিজেপির জন্য তা রাজনৈতিকভাবে বিপজ্জনক। মুসলিম রাষ্ট্রের সঙ্গে আলোচনার পথে গেলে দলের নির্বাচনী ভিত্তি নড়ে যেতে পারে। আগামী দুই বছরে অন্তত ১৩টি রাজ্যে নির্বাচন হবে, যার মধ্যে উত্তরপ্রদেশ রয়েছে — হিন্দু জাতীয়তাবাদের শক্ত ঘাঁটি।
তবে যুদ্ধের পথে গেলেও অর্থনৈতিক বিপর্যয় অনিবার্য। তাই কেন্দ্র সরকার পড়েছে এক অস্বস্তিকর জটে—যুদ্ধ করবে না বললে শক্তিহীন মনে হবে, আবার যুদ্ধ করলে সর্বনাশের ঝুঁকি। শেষ পর্যন্ত, ভারতের সামনে এখন কেবল একটাই প্রশ্ন—মোদি কি আবারও দলকে খাদের কিনারা থেকে ফিরিয়ে আনতে পারবেন? উত্তর সময় বলবে।



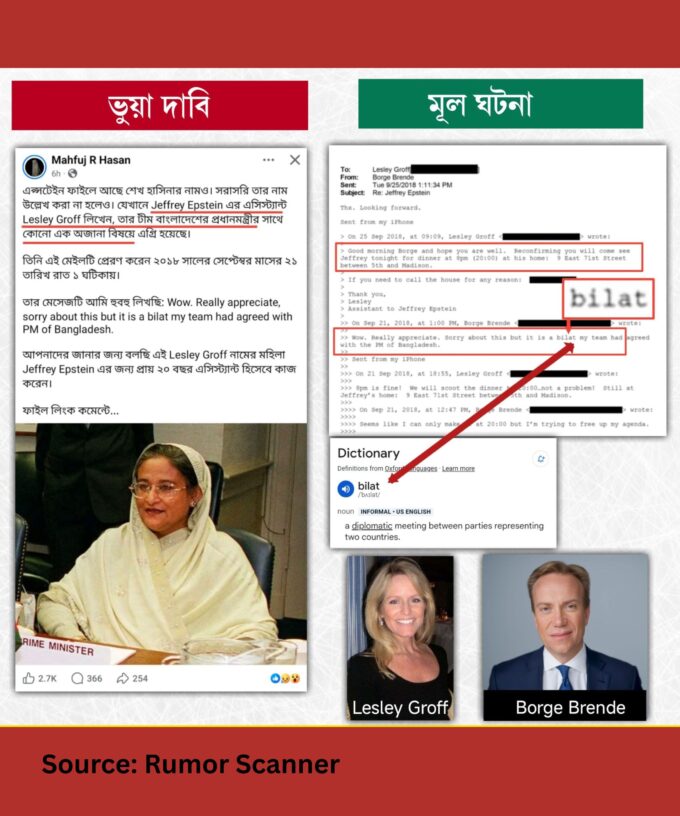





Leave a comment